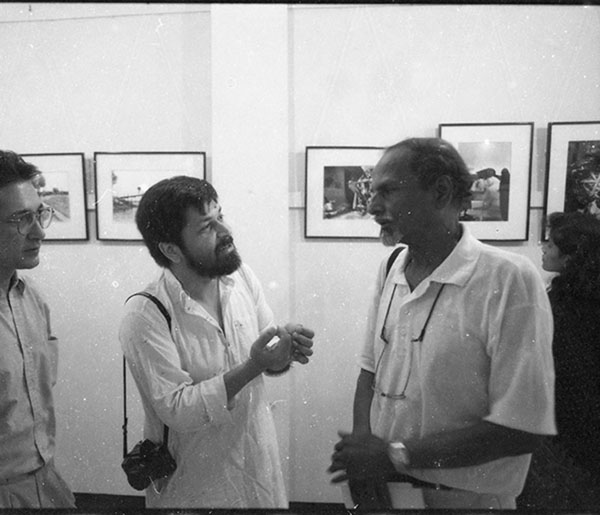কলোনিয়াল পোর্ট্রেট থেকে ডেভেলপমেন্ট ডিসকোর্স
নাঈম মোহায়মেন
…পূর্ব বাংলার ফটোগ্রাফিতে বাস্তবতার আগমনের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গেলে পেইন্টারদের প্রসঙ্গটা চলে আসে, বিশেষ করে জয়নুল এবং পরবর্তীতে কামরুলের ভূমিকা। এখানে কলোনিয়াল আমলের ফটোগ্রাফারদের লিগাসি নিয়ে বিড়ম্বনাটা আরেকটু তীক্ষ্ণ হয়। দেশ-বিভাগের আগে যে ফটোগ্রাফির ধারা চালু ছিল তা যথেষ্ট ভাবে এই বাংলার ফটোগ্রাফিকে রিয়ালিজমের দিকে টেনে নিতে পারেনি (যদিও কিছু ফটোগ্রাফি স্টুডিও স্থাপন হয়েছিল)। এবং এই শূন্যতার কারণেই জয়নুলের কাজের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
জয়নুলের ভূমিকার কথা বলতে গেলে মন্বন্তরের কাজটি (‘ফ্যামিন সিরিজ’) ভালমতো বুঝতে হবে, এবং বিশেষত সেই সময়কার প্রচলিত চারুকলায় এর প্রভাবটাকে খতিয়ে দেখতে হবে। সেই সময়ের প্রচলিত ধারার ব্যাপারে শোভন সোম লিখেছেন:
‘অ্যাকাডেমিক কেতার পুরোধা শিল্পীদের ছবিতে বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পেত নগ্নিœকা, অভিজাত বা ধনবান মানুষের অজুরায় আঁকা প্রতিকৃতি এবং অজুরায় আঁকা নানা বিষয়ের ছবি। বলা বাহুল্য, যেহেতু ছবি আঁকাই তাঁদের জীবিকার উপায় ছিল এবং সে সময় মুষ্টিমেয় ক্রেতাদের মধ্যে ছিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ বা বণিক এবং এই ক্রেতাদের রুচি-মাফিক না আঁকলে জীবিকার সুরাহা সম্ভব ছিল না, এ কারণে এই শিল্পীদের পক্ষেও নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে পা ফেলা কঠিন ছিল। ঐ সব বিষয় ছাড়াও এঁরা এক ধরনের দৃশ্য-চিত্র আঁকতেন যা ছিল রোম্যান্টিক আবেগে আপ্লুত, যেমন ঘনায়মান সন্ধ্যায় প্রান্তরে নামাজি, বনান্তরালে পল্লীবধূ, গোচারণ শেষে গো-পালসহ রাখাল-বালক ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বাস্তবতা-বর্জিত এই সব রোম্যান্টিক ছবির লক্ষ্য ছিল এক বিশেষ ধরনের ক্রেতা।’৪
এই প্রেক্ষিতটা লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, সেই সময়কার শিল্পীরা বাইরের পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবকে নিজেদের কাজে জায়গা দিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, কলকাতায় বিদেশি সৈন্যের আনাগোনা, গ্রামে- গ্রামে ক্ষুধার্ত মানুষ না খেয়ে মরছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে যামিনী রায় আঁকছে যিশু ও কৃষ্ণলীলার ছবি, যার খদ্দের কলকাতার উচ্চবিত্ত মানুষ অথবা আগন্তুক মার্কিন ও ইংরেজ সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার। একই সময়ে ক্যালকাটা গ্র“প বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিয়ে বরং দলীয় কর্মী-শিল্পী চিত্তপ্রসাদ, সূর্য রায়, রথীন মৈত্র ও সোমনাথ হোরকে পোস্টার আঁকার কাজে আটকে রেখেছেন। এমনকি নীরদ মজুমদারকে কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ তৈরির কাজে ব্যস্ত রাখা হয়।
এই নির্লিপ্ত শিল্প পরিস্থিতিতে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি কলকাতার ভদ্রলোক সমাজে একটা হাতবোমার মত বিস্ফোরিত হয়। শোভন সোমের ভাষায়ঃ
‘জয়নুলের ছবিতেও আমরা প্রতিবাদ দেখি না; যে সমাজব্যবস্থা এই দুর্ভিক্ষ তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে একটাও উত্তোলিত তর্জনী নেই। তার বিপ্রতীপে আছে নীরবে নিয়তিকে মেনে নেওয়া, আছে প্রতিবাদ-হীন মৃত্যু, কিন্তু প্রশ্ন নেই। তাঁর ছবির সামনে দাঁড়ালে দর্শক ভাবতে বাধ্য হন, কেন বিনা প্রশ্নে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এই পরিণাম মেনে নিল। আমরা দর্শক হিসাবে ভাবতে বাধ্য হই, যুগ যুগ ধরে এই দেশ কেন এইভাবে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। আর তখনই আমরা তাঁর ছবিতে নিজেদের স্বরূপ দেখে অনুভব করি যে, এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। তাঁর ছবিতে যা প্রতিবাদ-হীনতা বলে প্রতিভাত হয় বস্তুত তা প্রতিবাদকেই উসকে দেয়।’৫
জয়নুলের দুর্ভিক্ষ সিরিজের রূঢ়, মোটা, উগ্র, ড্রাই ব্রাশ স্ট্রোকগুলো নতুন এক ভাষার ইঙ্গিত দেয়। আলোচকরা বলেন যে, এই কাজের মধ্যে উঁচিয়ে ধরা মুঠিটা নেই। কিন্তু রাগ আছে প্রচুর। ভিক্ষুক, কুকুর, কাক এক জায়গায় মিলে গেছে ছবিগুলোতে। তাদের খাদ্য সন্ধানের স্থান এবং মৃত্যুর জায়গা মিলেমিশে আছে। হয়ত এক প্রজাতি মরলে সে অন্যের খাবারে পরিণত হবে। কলকাতার শিল্প-মহল জয়নুলের কাজ দেখে হতবাক হয় শুধু সোশাল রিয়ালিজমের থাপ্পড়ের জন্য নয়। তার সাথে যুক্ত হয় এই চিন্তাঃ ‘এ কোথা থেকে এলো, আমাদের প্রভাবের চিহ্ন পাচ্ছি না কেন?’ অনেকে তাকে বাক্সবন্দি করার জন্য ‘সোশাল রিয়ালিস্ট মুসলিম’ বলে আখ্যায়িত করে।
জয়নুলের সেই বড় ভাঙনের পর ফিরে যাবার পথ আর থাকে না। তার অনুগত কামরুল হাসান ও সফিউদ্দিনের কাজের সমন্বয়ে পেইন্টিংয়ের রোমান্টিক অতীতের সাথে একটা ভাঙন হয়ে যায়। ভারত বিভাগের পরে জয়নুলের প্রভাবে রিয়ালিজম পূর্ব পাকিস্তানের পেইন্টিংয়ে ঢুকে যায়। আমার ধারণা, এই জয়নুল স্কুল থেকেই রিয়ালিজমের ধারাটা ফটোগ্রাফির মধ্যে চলে আসে (বা, অনেকগুলো প্রভাবের একটা)। যেহেতু পূর্ববঙ্গের আলোকচিত্রে কলোনিয়াল বেঙ্গল ধারাটা দেশবিভাগের কারণে হারিয়ে যায়, ৫০ ও ৬০ দশকের ফটোগ্রাফি সেই কলোনিয়াল ধারাকে উপেক্ষা করে বরং চারুকলার জয়নুল ও অন্যান্যের প্রভাব গ্রহণ করে। পরের দশকের ফটোগ্রাফিতে বাস্তবতার উপস্থাপন জয়নুলের সেই ‘ফ্যামিন’ সিরিজের পরবর্তী ধাপ হিশাবে ভাবা যায়। যাত্রাপথে কোন এক সময়ে জয়নুলের এগ টেম্পেরা হয়ে যায় নাইব উদ্দিনের নেগেটিভ।